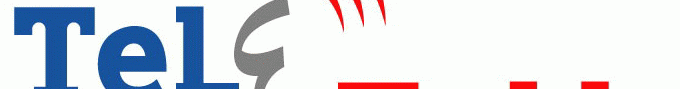মানব সভ্যতার ইতিহাসে যদি পূর্ণ হিসাবে কারও নাম বিবেচনা করতে হয়, তবে একটি নাম উচ্চারণ করতে হয়, তিনি লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি। এমন বহু বিচিত্র প্রতিভার সম্মেলন সম্ভবত অন্য কোনো মানুষের মধ্যেই দেখা যায়নি।
তিনি চিত্রশিল্পী, ভাস্কর, অঙ্কশাস্ত্রবিদ, গায়ক, প্রকৃতি বিজ্ঞানী, শারীরতত্ত্ববিদ, সামরিক বিশেষজ্ঞ, আবিষ্কারক, স্টেজ ডিজাইনার, দার্শনিক। প্রতিটি বিষয়েই তিনি চেয়েছিলেন শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে এবং অনেকাংশে তিনি সফলও হয়েছিলেন। এ যেমন একদিকে তার জীবনের গৌরব, অন্যদিকে ব্যর্থতা। তিনি মানবীয় সীমায়িত শক্তি নিয়ে চেয়েছিলেন ঈশ্বরের মতো সীমাহীন হতে। তাই সাফল্যের চূড়ায় উঠেও কখনো তৃপ্তি অনুভব করেননি। মনে হয়েছে তার জীবন এক অসমাপ্ত যাত্রাপথ। যে পথের শেষ তার কাছে অগম্যই রয়ে গেল।
ইতালির রেনেসাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ দ্য ভিঞ্চি বিধাতার পরিহাসে এক কুমারী নারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম ছিল পিয়েরো অ্যান্টনিও দ্য ভিঞ্চি। পিয়েরো ছিলেন উকিল। শৈশব থেকেই তার প্রতিভা বিকশিত হয়ে উঠেছিল। তার জীবনীকার লিখেছেন, অঙ্কে তার এত মেধা ছিল যে শিক্ষকরা তাকে পড়াত, তারা মাঝে মাঝেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ত। লিওনার্দোর অনুসন্ধিৎসা ছিল প্রবল। তার জিজ্ঞাসায় বিরক্ত হয়ে উঠত শিক্ষকরা। অঙ্ক ছাড়াও সঙ্গীতের প্রতি ছিল তার গভীর আকর্ষণ। বাঁশি বাজাতেন তিনি। পরবর্তীকালে যখন তিনি বাঁশি বাজাতেন এক স্বর্গীয় সুষমায় ভরে উঠত সমস্ত পরিমণ্ডল। তার কণ্ঠস্বরও ছিল সুমিষ্ট। তার গান শুনে সকলেই মুগ্ধ হতো।
সে যুগে চিত্রশিল্পকে কোনো সম্মানীয় হিসেবে গণ্য করা হতো না। তাছাড়া এতে ছেলের কোনো প্রতিভা আছে কিনা সে বিষয়েও পিয়েরো নিশ্চিত ছিলেন না। তাই লিওনার্দো যখন ছবি আঁকা শেখার অনুরোধ জানাল, সরাসরি তার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন।
লিওনার্দো উপলব্ধি করতে পারলেন বাবার অনুমতি ছাড়া ছবি আঁকা সম্ভব নয়। তাই একটি বুদ্ধি করলেন। একটা বড় কাঠের পাটাতনের ওপর গুহার ছবি আঁকলেন। গুহার মধ্যে আধো আলো আধো ছায়ার এক অপার্থিব পরিবেশ। তার সামনে এক ভয়ঙ্কর ড্রাগনের ছবি, তার মাথায় শিং। চোখ দুটো আগুনের মতো জ্বলছে। ভয়ঙ্কর হিংস্র দাঁতগুলো যেন ছুরির ফলা, নাক দিয়ে বেরিয়ে আসছে আগুনের লেলিহান শিখা।
ছবি আঁকা শেষ হতেই ঘরের মধ্যে ছবিটাকে রেখে সব জানালা বন্ধ করে দিলেন। পিয়েরো কিছুই জানেন না। ঘরে ঢোকামাত্রই সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে আতঙ্কে চিৎকার করে বেরিয়ে এলেন। পিয়েরো শান্ত হতেই লিওনার্দো গম্ভীর গলায় বললেন, আমি মনে হয় আমার যোগ্যতার প্রমাণ দিতে পেরেছি।
এবার আর ছেলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ করলেন না পিয়েরো। তিনি ছবি আঁকার অনুমতি দিলেন। সেই সময় ফ্লোরেন্সের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী ছিলেন ভেরক্কিয়ো। চিত্রশিক্ষার জন্য তার স্কুলে গেলেন লিওনার্দো। তখন তার বয়স আঠারো বছর।
লিওনার্দো শুধু ভেরক্কিয়োর কাছে ছবির আঙ্কিক শিক্ষা করেননি, তিনি দু চোখ মেলে দেখতে শিখেছিলেন প্রকৃতির অপরূপ রূপলাবণ্য, তার নিসর্গ শোভা, দেখেছেন নদীস্রোতের মধ্যে জীবনের প্রবাহ। তার সুখ, দুঃখ, ব্যথা-বেদনা শ্রদ্ধার গভীরে দেখেছেন নারীকে। ভেরক্কিয়োর কাছেই লিওনার্দো শিখেছিলেন কেমন করে মানব জীবনের গভীরে ডুব দিয়ে তার অপার রহস্যময়তাকে ফুটিয়ে তুলতে হয় রঙের তুলিতে। এই কারণেই লিওনার্দো ভেরক্কিয়োকেই তার গুরু হিসেবে স্বীকার করছেন। দুই বছর শিক্ষানবিশ শেষ করে লিওনার্দো স্থির করলেন নিজেই স্বাধীনভাবে শিল্পচর্চা করবেন। ফ্লোরেন্সে শিল্পীদের একটি সংঘ ছিল। তিনি তাতে নিজের নাম অন্তর্ভুক্ত করলেন।
ছবির পাশাপাশি চলছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার অধ্যয়ন। প্রকৃতপক্ষে তার মধ্যে ঘটেছিল বিজ্ঞানী আর শিল্পীর এক আশ্চর্য সংমিশ্রণ। তার চিন্তা কল্পনা অভিজ্ঞতা তার বিসতৃত বিবরণ লিখে রাখতেন খাতার পাতায়। দেখতে দেখতে দশ বছর ফ্লোরেন্সে কাটিয়ে দিলেন লিওনার্দো। এই সময় তিনি এঁকেছেন বেশ কিছু ছবি-অ্যানোনসেশন, মেরি ও যিশুর দুটি ছবি, এক রমণীয় প্রতিকৃতি।
ফ্লোরেন্সে থাকাকালীন সময়ে লিওনার্দো যে সমস্ত ছবি এঁকেছেন তার অধিকাংশই ছিল প্রচলিত শিল্পরীতির থেকে স্বতন্ত্র। তার এক শিল্পীর স্টুডিওর চার দেয়ালের মধ্যে বসেই সব ছবি আঁকতেন। লিওনার্দোই প্রথম শিল্পী যিনি প্রকৃতির ছবি আঁকার জন্য প্রকৃতির কাছে যেতেন। যা প্রত্যক্ষ করতেন তাকেই মনের রঙে রাঙিয়ে রূপ দিতেন। ছবির মধ্যে তিনিই প্রথম শেডের ব্যবহার আরম্ভ করেন।
লিওনার্দো স্থির করলেন, তিনি মিলানে যাবেন। মিলানের অধিপতি ছিলেন লুডোভিকো। ১৪৮২ সালে লিওনার্দো মিলানে এলেন। সেই সময় ফ্লোরেন্সের ডিউকের প্রাসাদে এক সঙ্গীত অনুষ্ঠনের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে লিওনার্দো তার বাঁশি বাজালেন। তার অসাধারণ সঙ্গীত প্রতিভায় মুগ্ধ হলেন ডিউক। তাকে নিজের প্রাসাদে আমন্ত্রণ করলেন। কয়েক দিনের পরিচয়েই ডিউক উপলব্ধি করতে পারলেন কী অসাধারণ প্রতিভাধর পুরুষ এই লিওনার্দো। তিনিই তাকে মিলানের অধিপতি লুডোভিকোর কাছে পত্র লিখতে অনুরোধ করলেন। লিওনার্দো লিখলেন তার সেই বিখ্যাত পত্র। এতে তিনি লিখলেন সামরিক প্রয়োজনে ৯টি মৌলিক সম্পূর্ণ নতুন আবিষ্কারের কথা।
মিলানের অধিপতি আমন্ত্রণ করে নিয়ে এলেন লিওনার্দোকে। প্রথম সাক্ষাতেই মুগ্ধ হলেন লুডোভিকো। লিওনার্দোকে নিজের রাজদরবারের অন্যতম প্রধান সভাসদ করে নিলেন। রাজপ্রাসাদেই তার থাকার আয়োজন করা হলো।
শুরু হলো লিওনার্দোর জীবনের আরেক অধ্যায়। দীর্ঘ আঠারো বছর লিওনার্দো ছিলেন মিলানে উদার হৃদয় লুডোভিকোর সাহচর্যে। এখানেই তার প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল। বহুদিন ধরেই লিওনার্দো কল্পনা করতেন এক আদর্শ শহরের। যে শহর হবে সর্বাঙ্গ সুন্দর, যেখানে মানুষের প্রয়োজনীয় সমস্ত সুযোগ-সুবিধা থাকবে। রাস্তা দুই ভাগে বিভক্ত। একদিকে মানুষ, যানবাহন যাবে, অন্যদিকে আসবে। শহর হবে ছোট। তাতে ৫ হাজারের বেশি বাড়ি থাকবে না। ছোট ছোট শহর রক্ষণাবেক্ষণ করা সহজ। শহর বড় হলে লোকসংখ্যা বাড়বে। তখন দেখা দেবে নানা সমস্যা। তাছাড়া শহরের সামর্থ্যের তুলনায় মানুষের সংখ্যা বেশি হলে তা হবে খোঁয়াড়ের মতো। অস্বাস্থ্যকর অসুবিধাজনক। শহরের কোনো নর্দমাই বাইরে হবে না। প্রতিটি নর্দমা হবে মাটির নিচে। সেখান দিয়ে শহরের সব আবর্জনা শহরের বাইরে নদীতে গিয়ে পড়বে।
লিওনার্দোর এই আদর্শ শহরের পরিকল্পনা সর্বযুগে সর্বকালেই প্রযোজ্য। কিন্তু ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও লুডোভিকো লিওনার্দোর এই পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে পারেননি।এরপর লিওনার্দো তৈরি করলেন নগরের ক্যাথিড্রালের এক সম্পূর্ণ নকশা। এসব কাজের অবসরে তিনি চর্চা করতেন জ্যামিতিক, জ্যোতির্বিদ্যা, অঙ্ক এবং এসব ক্ষেত্রে বহু মৌলিক চিন্তার প্রকাশ ঘটেছিল। এসব বৈজ্ঞানিক কাজকর্মের মধ্যেই তিনি পরিকল্পনা করেছিলেন লুডোভিকোর স্বার্থগত পিতার এক মূর্তি স্থাপন করার। সমস্ত পরিকল্পনা সমাপ্ত করার পর তিনি শুরু করলেন সেই অভূতপূর্ব বিশাল মূর্তি। উচ্চতায় ২৬ ফুট। একটি ঘোড়ার ওপর বসে আছেন স্বর্গত রাজা। মূর্তিটি তৈরি করতে সময় লেগেছিল আট বছর। এই সময় তিনি ম্যাডোনা নামে একটি ছবিও আঁকেন। এবার তাকে নতুন একটা কাজের ভার দিলেন লুডোভিকো। যিশুর জীবনের কোনো বিষয় নিয়ে ছবি আঁকতে হবে।
শুরু হলো লিওনার্দোর ভাবনা। কী ছবি আঁকবেন? দীর্ঘ ভাবনার পর স্থির করলেন যিশুর শেষ ভোজের ছবি আঁকবেন। চিত্রশিল্পের জগতে লাস্ট সাপার সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ছবি। ‘যিশু তার বারোজন শিষ্যকে নিয়ে শেষ ভোজে বসেছেন। তার দুপাশে ছয়জন ছয়জন করে শিষ্য। সামনে প্রশস্ত টেবিল। পেছনে জানালা দিয়ে মৃদু আলো এসে পড়েছে। যিশু বলেছেন তোমাদের মধ্যে কেউ একজন বিশ্বাসঘাতকতা করে আমাকে ধরে দেবে। শিষ্যরা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তারা সকলে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে তাদের মধ্যে কে বিশ্বাসঘাতকতা করবে’।
ছবিটি সান্তামারিয়া কনভেন্টের এক দেয়ালে আঁকা হয়েছিল। দি লাস্ট সাপার লিওনার্দোর এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। সমালোচকদের মতে, এখানে লিওনার্দোর মানসিকতা, তার ভাবনা কল্পনার সাথে মিলিত হয়েছে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি। লাস্ট সাপার শুধু যে একটি সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্র তাই নয়, মানুষের শিল্প প্রতিভা যে কোনো চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে এ তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ।
প্রথমে তিনি এঁকেছিলেন যিশুর বারোজন শিষ্যর মুখ। এই শিষ্যদের মুখে ফুটে উঠেছিল বিচিত্র অনুভূতি। কারও মুখে বিস্ময়, কারও মুখ ভয়, কারও বেদনা সন্দেহ। এক আশ্চর্য সুষমায় প্রতিটি মুখ জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। পরিশেষে তিনি আঁকলেন যিশুর মুখ। শোনা যায় কেমন হবে যিশুর মুখ, দীর্ঘ এক বছর তা স্থির করতে পারেননি। অবশেষে আঁকলেন যিশুর মুখ। এ মুখে ভয় নেই, ঘৃণা নেই, উদ্বেগ নেই। তিনি তো জানতেন তাকে ক্রুশবিদ্ধ হতে হবে। তার কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ঈশ্বরের ইচ্ছায় এবার তাকে মর্ত্যজগৎ ত্যাগ করতে হবে। ঈশ্বরের ইচ্ছাকে তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন। অনুভূতিহীন এক স্বর্গীয় ভাব ফুটে উঠেছে তার মুখে।
লাস্ট সাপার ছাড়াও আরও দুটি তৈলচিত্র এঁকেছিলেন লিওনার্দো। ভার্জিন অব দ্য রকস ও মেসিলিয়া। ১৪৯৯ খ্রিষ্টাব্দে ফরাসি সম্রাট মিলান আক্রমণ করলেন। তিনি মিলান ত্যাগ করে পালিয়ে এলেন ভেনিসে। ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দে মিলান সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়ে ফারসি অধিকারে চলে গেল। লিওনার্দো আশা করেছিলেন যুদ্ধ মিটে গেলে আবার মিলানে ফিরে যাবেন। কিন্তু যখন সেই আশা পূর্ণ হলো না তিনি ভেনিস ত্যাগ করে রওনা হলেন মাতৃভূমি ফ্লোরেন্সের দিকে। এই সময় সিজার বর্জিয়ার অনুরোধে মধ্য ইতালির বিসতৃত অঞ্চল পরিদর্শন করে ছয়টি ম্যাপ তৈরি করেন। সেই ম্যাপগুলো আজও উইন্ডসর লাইব্রেরিতে রক্ষিত আছে। সেগুলো দেখলে অনুমান করা যায় কি নির্ভুল ছিল তার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা এবং মানচিত্র অঙ্কন করার সহজাত দক্ষতা। ইতিপূর্বে তিনি একটি ছবি এঁকেছিলেন-ভার্জিন অব দ্য রকস। ঝুলে পড়া এক পর্বত। তার মধ্যে ফুটে উঠেছে চিরন্তন মানব আত্মার এক রূপ।
এই সময় লিওনার্দো আঁকলেন তার জগৎ বিখ্যাত মোনালিসা। এই ছবিটি আঁকতে তার তিন বছর সময় লেগেছিল। কে এই মোনালিসা এ বিষয়ে ভিন্নমত আছে। কয়েকজনের অভিমত মোনালিসার প্রকৃত নাম ছিল লিজা। তিনি ছিলেন ফ্লোরেন্সের এক অভিজাত ব্যক্তির স্ত্রী। ভিন্ন মত অনুসারে মোনালিসা ছিলেন জিয়োকোন্ত নামে এক ধনী বৃদ্ধের তৃতীয় পত্নী। নাম মাদোনা এলিজাবেথ। দিনের পর দিন অসংখ্য ভঙ্গিতে মুখের ছবি এঁকেছেন। কিন্তু কোনো ছবিই তার মনকে ভরিয়ে তুলতে পারেনি। একদিন লিওনার্দোর চোখে পড়ল এলিজাবেথের ঠোঁটের কোনায় ফুটে উঠেছে বিচিত্র এক হাসি। চমকে উঠলেন লিওনার্দো। এই হাসির জন্যই যেন তিনি তিন বছর অপেক্ষা করেছিলেন। মুহূর্তে তুলির টানে ফুটিয়ে তুললেন সেই সহাস্যমণ্ডিত কালজয়ী হাসি। চিত্রশিল্পী হিসেবে লিওনার্দোর খ্যাতি জগৎ বিখ্যাত হলেও তার মৃত্যুর পর পাওয়া গিয়েছিল প্রায় পাঁচ হাজার পাতার হাতের লেখা পাণ্ডুলিপি। এই পাণ্ডুলিপিতে তিনি সমস্ত জীবন ধরে যেসব পর্যবেক্ষণ করেছিলেন পরীক্ষা করেছিলেন, তারই বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। এই পাণ্ডুলিপি লেখা হয়েছিল ইতালিয়ান ভাষায় এবং সমস্ত পাণ্ডুলিপিটাই লেখা হয়েছিল উল্টো করে। ফলে সোজাসুজি পড়া যেত না। পড়তে হতো আয়নার মাধ্যমে। প্রতিটি লেখার সঙ্গে থাকত অসংখ্য ছবি।
তার এই পাণ্ডুলিপিতে অসংখ্য বিষয় নিয়ে লেখা হয়েছে। চীন উপকথা, মধ্যযুগীয় দর্শন, সমুদ্রস্রোতের কারণ, বাতাসের গতি, তার চাপ, পৃথিবীর ওজন। নিশাচর পাখির গতিপ্রকৃতি। পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব। উড়ন্ত যান। সাঁতার কাটার যন্ত্র। আলোর প্রকৃতি, যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্রের নকশা। সুগদ্ধ সেন্ট তৈরির ফর্মুলা। বিভিন্ন পাখি জন্তু-জানোয়ারের আচার-আচরণ, বিভিন্ন গাণিতিক সূত্র।
তার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা এত গভীর ছিল যে গোপনে বেশকিছু মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করে দেখেছিলেন দেহের গঠন। তার এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বেশ কিছু শারীরতত্ত্বের ছবি এঁকেছিলেন। সেই ছবি এত নির্ভুল ছিল, পরবর্তীকালে চিকিৎসকরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। আধুনিক উড়োজাহাজের তিনিই প্রথম নকশা আঁকেন। তার পাণ্ডুলিপির এক জায়গায় লিখেছেন একদিন মানুষ আকাশে উড়বেই।
লিওনার্দোর মৃত্যুর প্রায় আড়াইশ বছর পর একজন পন্ডিত তার পাণ্ডুলিপির সম্পূর্ণ পাঠ উদ্ধার করে চৌদ্দটি খণ্ডে প্রকাশ করে। দীর্ঘ ছয় বছর লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি ফ্লোরেন্সে কাটিয়ে দিলেন কিন্তু শেষ দিকে তার আর ফ্লোরেন্স ভালো লাগছিল না। তিনি ফিরে গেলেন মিলানে। মাঝে মাঝে ফ্লোরেন্সে যেতেন। ১৫১৬ সালে লিওনার্দো ফারসি সম্রাটের আমন্ত্রণে প্যারিসে গেলেন। সম্রাট লিওনার্দোকে খুবই সম্মান করতেন। ক্রমশই স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ছিল। ডান হাত অকর্মণ্য হয়ে গিয়েছিল। বাঁ হাতেই তিনি ছবি আঁকতেন। এই সময় তিনি ঈশ্বরের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন। অবশেষে ৬৭ বছর বয়সে ২ মে ১৫১৯ সালে চিরদিনের জন্য পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি-ইতালীয় রেনেসাঁসের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ।
বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ১০০ মনীষীর জীবনী থেকে
(খ্রিষ্টপূর্ব ১৪৫২-১৫১৯)